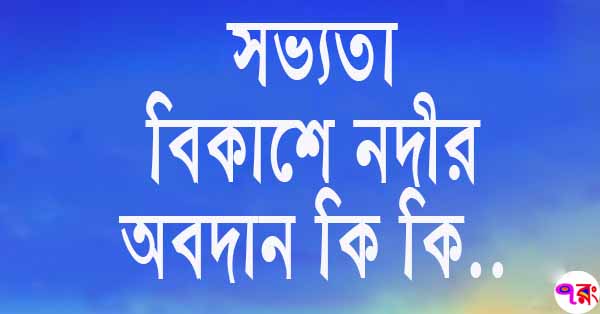প্রিয় পাঠক, প্রত্যকটি সভ্যতা বিকাশে কোনো না কোনো ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক উপাদানের অবদান রয়েছে। ঠিক তেমনি করে বিশ্বের অনেক বিখ্যত সভ্যতা বিকাশে নদীর অবদান রয়েছে।
যেমন মিশর, পারস্য সিন্ধু সহ বেশ কিছু সভ্যতা বিকাশে নদীর অবদান জেনে নিব।
মিশরীয় সভ্যতা বিকাশে নদীর অবদান:
মিশরের ভৌগােলিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে হেরােডােটাস বলেছেন- মিশর হলো নীলনদের দান! মধ্য আফ্রিকার উচ্চ ভূমিতে উৎপন্ন হয়ে নীলনদ ভূমধ্যসাগরে পতিত হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রায় ৭৫০ মাইল প্রবাহিত হয়েছে।
ফলে নীলনদের পানি সঞ্চিত হয়ে বদ্বীপের ১২,৫০০ মাইল এলাকা কৃষিযােগ্য ভূমিতে পরিণত হয়েছিল।
প্লাবনের সময় নীল অববাহিকায় পলি সঞ্চিত হয়ে উচ্চ হয়ে উঠত। এজন্য কৃষি কাজের জন্য এ উর্ধ্ব ভূখণ্ডে গড়ে উঠেছিল জনবসতি, অববাহিকায় পলি সঞ্চিত হয়ে বা বাঁধ দিয়ে অনেকে কৃষিকাজ করতাে।
এছাড়াও বাঁধ নির্মাণ কার্য পরিচালনার জন্য কারিগর, শ্রমিক, পরিচালক সহ অনেক ধরনের মানুষের দরকার হতাে।
অপরদিকে নগরবাসী ও কারিগররা, কৃষিজীবী মানুষের উৎপন্ন উদ্বৃত্ত শস্য খেয়ে বেঁচে থাকতে পারত! এ সুযােগ সৃষ্টি হওয়ার পর সভ্যতার জন্ম হয়েছিলো! মােহনার কাছাকাছি অববাহিকায় ছিল প্যাপিরাস জাতীয় নলখাগড়ার জঙ্গল, খেজুর, ডুমর ইত্যাদি সহ নানা গাছ।
এসব গাছ থেকেও খাদ্য, ঘরবাড়ি তৈরির প্রচুর সরঞ্জাম পাওয়া যেত।
মিশরের পার্বত্য অঞ্চলে গ্রানাইড, চুনাপাথর ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে ছিল! আর সুরিয়ান পাহাড়ে ছিল প্রচুর সােনা।
নীল নদীর অববাহিকায় এ উর্বর জমি প্রাকৃতিক সম্পদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা।
মেসােপটেমীয় সভ্যতা বিকাশে নদীর অবদান:
টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর জলধারাকে কেন্দ্র করে এ দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে ব্যাবিলনীয়, এসেরীয়, সুমেরীয় ও ক্যালডীয় প্রভৃতি সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল, যাকে এককথায় বলা হয় মেসােপটেমিয়া সভ্যতা। প্রতি বছর মার্চ থেকে জুলাই পর্যন্ত বরফগলা পানিতে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটি নদীর দুই তীর প্লাবিত হয়ে যেত ফলে তীরে পলি জমত এবং এখানকার উর্বর ভূমি ছিল কৃষি কাজের উপযােগী।
এ অঞ্চলে প্রচুর চুনাপাথর ও কাদামাটি ছিল। উল্লেখযােগ্য পাহাড়সমূহে ছিল গবাদি পশু, ছাগল, সিংহ এবং নিচে ছিল প্রচুর মাছ। তাই এ ভূখণ্ডের উত্তরে আমােনয়ার পার্বত্যাঞ্চল, দক্ষিণ-পূর্বে পারস্য উপসাগর, পূর্বে এলাম পাবর্ত্যাঞ্চল এবং পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর অবস্থিত ছিলো। দুই নদীর উৎসসমূহ থেকে শুরু করে পারস্য উপসাগরে পতিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নদী দুটি নৌ বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।
তাই বলতে পারি মেসােপটেমীয় সভ্যতা গঠনে নদীর বিশেষ অবদান ছিলো।
সিন্ধু সভ্যতার বিকাশে নদী:
প্রাচীন ভারতের পঞ্চনদ বিধৌত অঞ্চল পাঞ্জাব ও ইন্ডাস নামে পরিচিত ছিলো! সিন্ধুনদ বিধৌত অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতা।
নদী তীরের উর্বর ভূমির অনুকূলে এবং পরিবহনে সুযােগ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে এ সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল।
তাই ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ রপ্তানি ও বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সিন্ধুর বন্দরগুলাে ব্যবহৃত হতাে।
পারস্য সভ্যতা বিকাশে নদীর অবদান:
প্রাচীন পারস্য সভ্যতার উন্মেষে সেখানকার নদী ও সম্পদ বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। অপরদিকে আরব মরুভূমির সীমান্ত রেখায় দক্ষিণাঞ্চলীয় তৃণভূমি ও দানিয়ুব নদীর নিম্ন অঞ্চলের পূর্বদিকে এবং কৃষ্ণ সাগরের উত্তর প্রান্ত থেকে দক্ষিণ রাশিয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ উত্তরাঞ্চলীয় তৃণভূমি যাযাবর মানুষদের বসতি গড়ে তােলার উৎসাহ যােগায়।
উপকূলীয় পর্বত শ্রেণীতে কৃষি ও চাষের পক্ষে বাধাস্বরূপ হলেও পর্বতের পাদদেশে বনজ সম্পদ সহ সােনা, রুপা, লােহা, তামা, সিসা ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে ছিল! দেশের অভ্যন্তরে গম, যব ইত্যাদির চাষ ও পশুপালনের সুবিধা ছিল।
গ্রিক সভ্যতার বিকাশে নদীর ও সাগরের ভূমিকা:
গ্রিসের সভ্যতা বিকাশে সমুদ্রের প্রভাব ছিল অপরিসীম। গ্রিসের তিনদিকের উপকূল আর্ডিয়াটিক সাগর, ভূমধ্যসাগর, ইজিয়ান সাগর বিধৌত।
এশিয়া মাইনরের নৈকট্য এবং ইজিয়ান এর বক্ষে অসংখ্য দ্বীপমালার অস্তিত্ব গ্রিকদের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যে উৎসাহিত করে তুলেছিল।
ফলে গ্রিসের খনিজ সম্পদ যেখানে লােহা, রুপা, সােনা, কাদামাটি, মার্বেল পাথর ছিল সেখানে ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার ও কারিগরি শিল্পে সহায়তা করেছিল।
রােমক সভ্যতা গঠনে নদীর ভূমিকা:
পূর্ববর্তী অন্যান্য সভ্যতার মত রােমক সভ্যতা গড়ে উঠার পিছনেও তার ভৌগােলিক অবস্থার প্রভাব ও নদ নদীর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে! যেমন টাইবার নদী ভূমধ্যসাগর, এড্রিয়টিক সাগর, ইট্রাকান সাগর, রােমক সভ্যতা বিকাশে সাহায্য করেছিল।
প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ;পাথর, তামা, সােনা, লােহা প্রভৃতি কারিগরি শিল্প বিকাশে ও বহির্বাণিজ্যে সহায়তা করেছিল! উর্বর জমি থাকার কারণে এখানে কৃষিক্ষেত্রের বিকাশ ঘটেছিল।
চৈনিক সভ্যতার পেছনে নদীর অবদান:
চীনের তিনটি প্রধান অঞ্চলকে ঘিরে সভ্যতার চারণভূমি গড়ে উঠেছিল। প্রথমটি হােয়াংহাে নদীর তীরবর্তী অঞ্চল আর দ্বিতীয়টি ইয়াংসিকিয়াং নদীর তীরবর্তী অঞ্চল এবং তৃতীয়টি দক্ষিণ চীনের ভূখণ্ড।
হােয়াংহাে নদীর ও ইয়াংসিকিয়াং নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের উর্বরতা ও পরিমিত বৃষ্টিপাত চীনের কৃষি সভ্যতাকে অনেকটা এগিয়ে নিয়েছিল। অন্যদিকে বহির্বাণিজ্য পর্যন্ত হয়েছিল উন্মুক্ত। দক্ষিণ চীনের পার্বত্যাঞ্চল তামা, টিন, সীসা প্রভৃতি খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল। তাই বলা যায় চীন সভ্যতার পেছনে নদীর বিশেষ অবদান ছিলো।
বিভিন্ন সভ্যতায় নদীর বিশেষ বিশেষ অবদান সমূহ:
নদী তীরবর্তী সভ্যতা কষিপ্রধান। তাই কষি ছিল এসব সভ্যতার জীবনীশক্তি। আসলে কষির প্রয়ােজনে তথা উর্বর জমি ও জলসেচের সুবিধার জন্য প্রাচীন সভ্যতা নদীর তীরে কেন্দ্রীভূত হয়ে গড়ে উঠেছিল।
কৃষির ভিত্তি ছিল জলসেচ ব্যবস্থা। ফলে কষি কাজের জন্য নদীগুলাে থেকে সেচব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। আর যেহেতু তখন অর্থনীতি ছিল কৃষিনির্ভর, তাই বলা যায় সেসব সভ্যতার অর্থনীতি ছিল সেচব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল।
সুবিন্যস্ত জলসেচ প্রণালী নদী তীরবর্তী সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিলো।
নদী তীরবর্তী সভ্যতাতে ব্যক্তিগত মালিকানা ও সামাজিক শ্রেণীবিভাগ সৃষ্টি হয়েছিল।
তাই সভ্যতাগুলােতে আমরা শ্রেণি প্রথা সহ শাসন ও শোষণের চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। যেমন উচু শ্রেণীতে ছিল রাজা, পুরােহিত এবং তাদের অনুচর পাত্র, মিত্র ও ধনী ভূমির মালিক আর নিচু শ্রেণীতে ছিল ভূমিদাস ও ক্রীতদাস। ক্রীতদাস প্রথা প্রাচীন সভ্য সমাজগুলাের অপরিহার্য অঙ্গ ছিলো।
এছাড়া জলসেচের প্রয়ােজনীয়তার কারণে ক্ষমতাশালী কেন্দ্রীয় রাজশক্তির উদ্ভব হয়েছিল এবং বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল। সুগঠিত আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে স্বৈরাচারী রাষ্ট্রশক্তি জলসেচ ব্যবস্থা বলবৎ রাখতে সক্ষম হয়েছিল।
এসকল কারণে ইতিহাসবিদগণ নদী তীরবর্তী সভ্যতাগুলাের রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে স্বৈরতন্ত্র (Despolism), শাসনব্যবস্থাকে Agroburaucracy এবং সমাজব্যবস্থাকে জলনির্ভর সমাজ নামে চিহ্নিত করেছেন।
নদী তীরবর্তী সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র কতকগুলাে নগর, রাজধানী, ধর্মস্থান বা ব্যবসায়কেন্দ্র নগর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর নগরগুলােই সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছিল! সমাজের কর্ণধার, যেমন রাজা, পরিষদ, পুরােহিত সহ ভূমি অধিকারীরা নগরে বসবাস করত।
সুতরাং নদী তীরবর্তী সভ্যতাকে নাগরিক সভ্যতা বলা চলে।
অপরদিকে নদী তীরবর্তী সভ্যতাগুলাের উপর ধর্মের অসামান্য প্রভাব ছিল।
সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ধর্মের গুরুত্ব ছিল প্রবল।
ধর্মীয় অনুশাসন ও বিধি নিষেধে সমাজ জীবন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়েছিল এবং কৃষি ভূমির মাধ্যমে পুরােহিত শ্রেণী অর্থনৈতিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করত।
ফলে রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ ছিল না। ধর্ম ও রাষ্ট্র ছিল অভিন্ন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজা ছিলেন প্রধান পুরােহিত।
উপরের আলোচনার আলোকে আমরা বলতে পারি সভ্যতা বিকাশে নদী শুধু অসামন্য অবদানই রাখেনি, নদী প্রত্যক সভ্যতার অর্থনীতি, সমাজ ব্যবস্থা, প্রশাসন সহ ধর্মকেও নিজ হাতে গড়ে দিয়েছিলো।